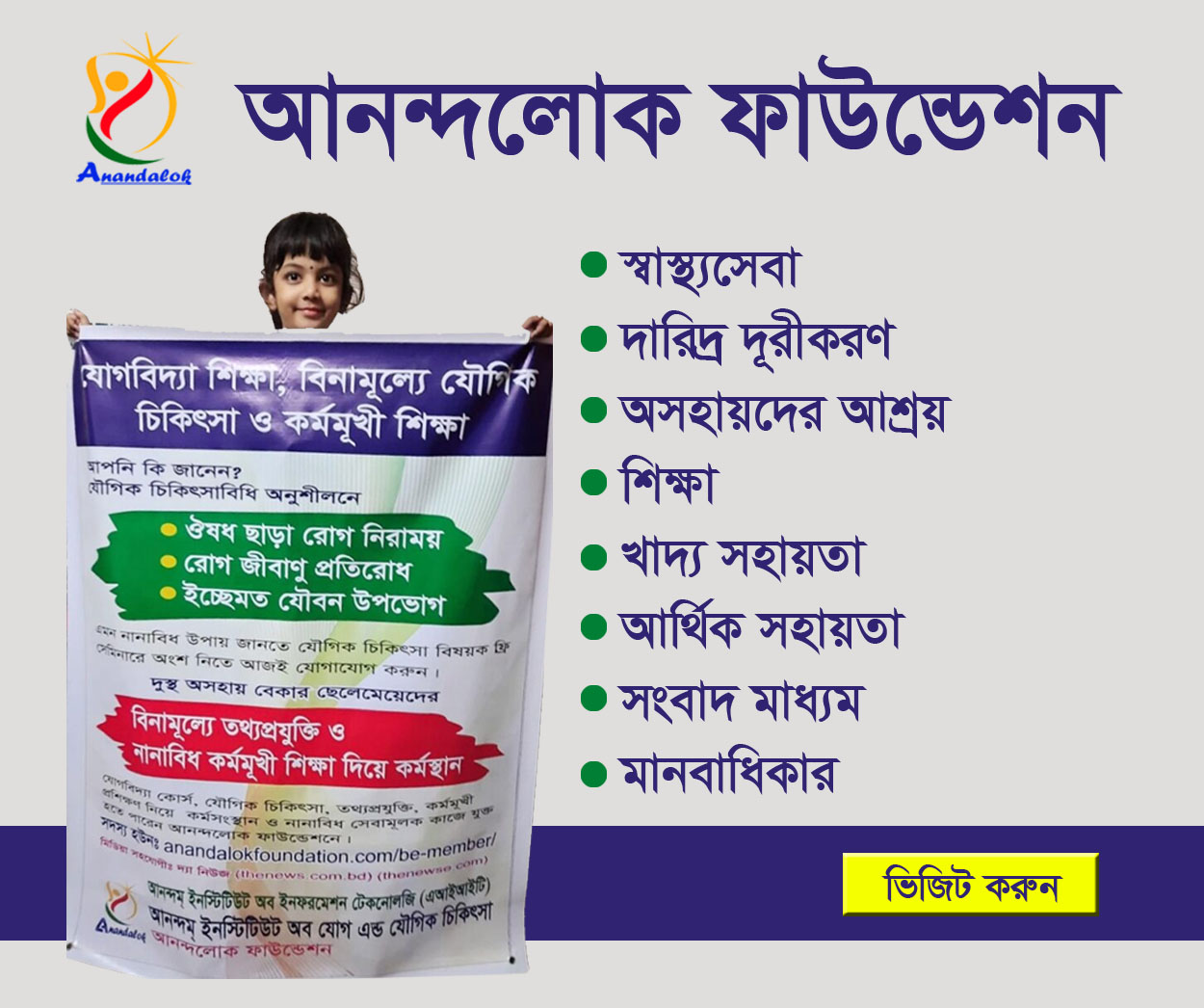আজ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ১৫২তম জন্মদিন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে সম্প্রীতি আর ঐক্যে এক অবিস্মরণীয় নাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। নানা ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ, জাত-বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার ঊর্ধ্বে রাজনীতির পক্ষে অবিচল ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। এই অসামান্য ত্যাগের জন্য ভারতবর্ষের জনগণ কর্তৃক তিনি ‘দেশবন্ধু‘ উপাধিতে ভূষিত হন।
১৮৭০ সালের ৫ নভেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহন করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর পিতা ভুবনমোহন দাশ একজন আইনজীবী ছিলেন এবং মা নিস্তারিণী দেবী গৃহিনী। চিত্তরঞ্জন দাশের পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামে। শিক্ষিত পরিবার হিসেবে তাঁদের পরিবারের যথেষ্ঠ সুনাম ছিল। চিত্তরঞ্জন দাশের পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। প্রাথমিক পড়াশুনা শেষ হওয়ার পূর্বে চিত্তরঞ্জন দাশ শৈশবে তাঁর বাবার সাথে কলকাতার ভবানীপুরে চলে আসেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ১৮৭৯ সালে ভবানীপুর লন্ডন মিশানারি স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলের পাঠ্যবই পড়ার চেয়ে পাঠ্যতালিকার বাইরের বই পড়তে বেশী পছন্দ করতেন তিনি। যে কারণে তাঁর পরীক্ষার ফলাফল খুব ভাল হতো না। চিত্তরঞ্জন দাশ ১৮৮৬ সালে লন্ডন মিশানারি স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। এরপর ভর্তি হন প্রেসিডেন্সী কলেজে। এই কলেজে পড়ার সময় তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৮৯০ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেত যান। বিলেতে থাকার সময় রাজনৈতিক ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৯৩ সালে ব্যারিস্টারি পড়া শেষ করে দেশে ফিরে আসেন এবং আইন পেশা শুরু করেন। ১৮৯৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসেবে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত হয়। পেশা জীবনের শুরুতে তাঁর সামান্য আয় হত। যা দিয়ে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ট্রামভাড়ার সামান্য পয়সা বাঁচানোর জন্য তিনি হাইকোর্ট থেকে ভবানীপুর হেঁটে যেতেন। আইন পেশার পাশাপাশি গোপনে গোপনে বিপ্লবী রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। ১৯০৩ সালে কলকাতায় প্রমথ মিত্র ও চিত্তরঞ্জন দাস প্রথমে ‘অনুশীলন সমিতি‘ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত তিনি এই সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের ‘বন্দে মাতরম’ পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল।
ওকালতি করেও যে দেশপ্রেমের পরিচয় দেয়া যায়, তা দেখা যায় আইনজীবী চিত্তরঞ্জনের জীবন থেকে। রাজনৈতিক বন্দীদেরকে তাদের বিরুদ্ধে আনীত মারাত্মক অভিযোগের হাত থেকে তিনি মুক্ত করে আনতেন তার অসাধারন মামলা পরিচালনার গুনে। চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯০৬ সালে যোগদান করেন নাগপুর কংগ্রেসে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহন করার জন্য তিনি আইন ব্যবসা সম্পূর্নরূপে বন্ধ করেন। আইনজীবী হিসেবে চিত্তরঞ্জন দাশের জন্য ১৯০৭ সাল ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সময় তিনি সিভিল ও ক্রিমিনাল উভয় কোর্টেই একজন সফল আইনজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিস্থাপন করেন। এ সময় কলকাতা কোর্টে দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের যত মামলা এসেছে তিনি সেগুলোর বিরুদ্ধে অবিরাম লড়েছেন। শুধু আইনের জগতে নয় , সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন সাহিত্য চর্চায় মগ্ন। রাজনীতির মধ্যে থেকেও তিনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। সে সময়ের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা ‘নারায়ণ’-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন তিনি। ‘মালঞ্চ’, ‘সাগর সঙ্গীত’ ও ‘অন্তর্যামী’ গ্রন্থের জন্য তিনি কবি ও লেখক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।
প্রবীণ কংগ্রেসীদের মতো বিলেত ফেরৎ নামী ব্যারিস্টার হলেও চিত্তরঞ্জন রাজনীতির ভাষা হিসেবে ইংরেজীর জায়গায় বাংলাকে স্থান করে দিলেন। পাশাপাশি বাংলার দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু মুসলিমের ঐক্যের জায়গাটিতে সবচেয়ে বেশি জোর দিলেন।
মর্লে মিন্টো সংস্কারের মধ্য দিয়ে আসা পৃথক ধর্মভিত্তিক নির্বাচন এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে হিন্দু মহাসভার জন্ম হয়েছিল ১৯০৯ সালে। হিন্দু সমাজের ভেতর থেকে নানা উগ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং মর্লে মিন্টো সংস্কারে ধর্মভিত্তিক নির্বাচনের প্রস্তাব এলে তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণি, যারা ছিল মূলত উচ্চবর্ণ হিন্দু, তারাই বেশি সংখ্যায় সেসময় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিলেন। এই ভদ্রলোক শ্রেণি তাদের ক্ষমতা হারানোর ভয় থেকে কীভাবে অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্নে এককাট্টা হয়েছিল, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন জয়া চ্যাটার্জী তাঁর বেঙ্গল ডিভাইডেড বইতে। অন্যদিকে চরম উগ্রবাদীরা মনে করেছিলেন হিন্দুদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন দরকার এবং কংগ্রেস তা হতে পারে না। এই ভাবনা থেকেই হিন্দু মহাসভা জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু হিন্দু মহাসভা সে সময়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয় নি। ধর্মীয় উন্মাদনার মুখে দাঁড়িয়েও হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি সংক্রান্ত সঙ্কটের বাস্তব দিকগুলিকে বোঝবার ও তার ভিত্তিতে আন্তরিকভাবে কাছাকাছি আসার একটা আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের মধ্য, আর এই এই গোটা প্রক্রিয়ার পুরোভাগে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গোরা, ঘরে বাইরের মত উপন্যাসে বা অসংখ্য কবিতায় প্রবন্ধে হিন্দু সমাজের মধ্যেকার জরুরী আত্মসমালোচনার কাজটা শুরু করেছিলেন তিনি। মহাত্মা গান্ধীর জাতীয় রাজনীতিতে আবির্ভাবের পর, বিশেষত গণ আন্দোলনের পর্ব শুরু হলে ধর্মীয় উগ্রতার পরিবেশ অনেকটা কমে আসে। লক্ষনৌ চুক্তি (১৯১৬) র সূত্রে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সামনের সারির নেতারা প্রথমবারের জন্য কাছাকাছি আসেন এবং সম্প্রীতি ও সমঝোতার পরিবেশ তৈরি হয়। সম্প্রীতির পরিবেশ আরো জোরালো হয় ১৯১৯ এ অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন একযোগে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করলে। সম্প্রীতির পরিবেশ হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির জমিকে অনেকটাই কেড়ে নেয়।
১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইনসভা বর্জন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি নিজেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কংগ্রেস অধিবেশনে উত্থাপন করেন এবং গান্ধীজীর ডাকে ব্যারিস্টারি পেশা ত্যাগ করে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বয়ং ভারত সরকার প্রখ্যাত মিউনিশনস বোর্ড ঘটিত মামলায় প্রচলিত নজীর উপেক্ষা করে সাহেব এডভোকেট জেনারেল অপেক্ষা অধিক পারিশ্রমিক দিয়ে তাঁকে সরকারি কৌসুলী নিযুক্ত করেন। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি এ দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। এই অসামান্য ত্যাগের জন্য ভারতবর্ষের জনগণ কর্তৃক তিনি ‘দেশবন্ধু‘ উপাধিতে ভূষিত হন।
১৯২২ সালে চৌরিচৌরার একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার আকস্মিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন গান্ধীজী। অচিরেই ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলনে শুরু হয় ভাঁটার পর্ব, হিন্দু মুসলিম ঐক্য ভেঙে পড়ে এবং এই পর্বেই ১৯২৫ এ জন্ম নেয় আর এস এস, নতুন করে বিকশিত হয় হিন্দু মহাসভা।
সাম্প্রদায়িক বিরোধকে আরো বাড়িয়ে তোলার কাজটা একদিকে হিন্দু মহাসভা, আর এস এর মতো সংগঠনগুলি করতে চাইছিল সাভারকর, হেডগাওয়ার প্রমুখদের নেতৃত্বে এবং মুসলিম লীগের একাংশের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাচ্ছিল। কংগ্রেসের অনেক নেতাও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে যথেষ্ট বিপদজনক অবস্থান নিচ্ছিলেন। এই জটিল ও বিপদজনক সময়ে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে হিন্দু মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজটা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে করতে চেয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁর অনুগামীরা। কংগ্রেসের ভেতর থেকেই তাঁরা স্বরাজ্য দল বলে আলাদা একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে এই ব্যাপারে এগিয়ে ছিলেন।
স্বরাজ্য দল তৈরির প্রয়োজন চিত্তরঞ্জন অনুভব করেন গান্ধীর নেতৃত্বাধীন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের বেশ কিছু রণকৌশলের বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস আইনসভা বর্জন করে। অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন চলাকালে এই নীতি দেশবাসীকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। কিন্তু চৌরিচৌরার ঘটনার পর গান্ধীজী অকস্মাৎ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর এক নতুন পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস জেলে থেকেই আন্দোলনের নতুন কর্মপদ্ধতির কথা চিন্তা করেন। তিনি ইতিপূর্বে কংগ্রেসে গৃহীত আইনসভা বর্জনের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে অবিলম্বে আইনসভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর মতে কংগ্রেসের উচিত নির্বাচনে যোগদান করে আইনসভার সব আসন ও সেই সঙ্গে অন্যান্য স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচিত আসনগুলি দখল করা। এভাবে সরকারি ক্ষমতা করায়ত্ত করে যথাসম্ভব গঠনমূলক কাজকর্মে ব্রতী হওয়া ও আইনসভায় অংশগ্রহণ করে নিরন্তর বাধাদানের মাধ্যমে সরকারি কাজকর্মে অচলাবস্থার সৃষ্টি করা ছিল তাঁর রাজনৈতিক রণকৌশল। চিত্তরঞ্জন দাসের এই নতুন পরিকল্পনা আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি নেতাদের অনেকেরই পছন্দ হয়। অনেকে আবার গান্ধীজীর অসহযোগ নীতি চালিয়ে যাবার পক্ষপাতি ছিলেন । এ নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে দুটি গোষ্ঠির উদ্ভব হয়। যাঁরা চিত্তরঞ্জন দাসের নতুন পরিকল্পনার সমর্থক তাঁরা পরিবর্তনকামী নামে পরিচিত হলেন। মতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, বিটলভাই প্যাটেল, এন.সি. কেলকার, হাকিম আজমল খাঁ, সত্যমূর্তি জয়াকর প্রমুখ এই মতের সমর্থক ছিলেন। অন্য যাঁরা এই মতের বিরোধী ছিলেন তাঁরা পরিবর্তন বিরোধী রূপে পরিচিত হলেন। চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কে.আর. আয়েঙ্গার, ডক্টর আনসারি, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতা এই দলে ছিলেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে পরিবর্তনকামী গোষ্ঠী তাঁদের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল তর্কাতর্কি হয়। শেষে পরিবর্তনকামীরা তাঁদের প্রস্তাব অনুমোদন করাতে ব্যর্থ হওহায় এই অধিবেশনের সভাপতি তথা নতুন পরিকল্পনার রূপকার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কংগ্রেস ত্যাগ করেন ও ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তাঁর নেতৃত্বে ‘স্বরাজ্য দল’ গঠিত হয়।
১৯২৩ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে মতিলাল নেহেরুর সহযোগীতায় স্বরাজ দল গঠন করেন। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সাধনের জন্য তাঁর নেতৃত্বে স্বরাজদল মুসলিম নেতাদের সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের অধিকার বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করে। চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহরু যথাক্রমে এর সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হন। তারপর এই দলের সদস্যগণ সারা ভারত পরিভ্রমণ করে স্বরাজ্য দলের নীতি ও কর্মসূচি জনসমক্ষে প্রচার করেন।
স্বরাজ্য দলের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি ছিল —
(১) নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভায় যোগদান করে সভার কাজকর্মে অবিরাম বাধাদান করে প্রশাসনিক অচলাবস্থা তৈরি।
(২) সরকারি বাজেট প্রত্যাখ্যান করে জাতীয় বাজেট গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করা ।
(৩) নানা প্রকার বিল ও প্রস্তাব উত্থাপন করে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি ঘটাতে সাহায্য করা ।
(৪) জাতীয় স্বার্থে নতুন অর্থনীতি রচনা করে বিদেশি অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করা ।
(৫) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভ করা প্রভৃতি ।
বাংলার প্রাদেশিক রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জন দাশ সবচেয়ে বেশি জোর দেন হিন্দু মুসলিম ঐক্যের দিকটির ওপর। দেশবন্ধুর অভিমত ছিল যে, বঙ্গীয় আইন পরিষদে বলিষ্ঠ গ্রুপ সৃষ্টিকারী মুসলিম সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতিরেকে স্বরাজবাদীদের বাধাদানের নীতি সফল হবে না। বস্তুতপক্ষে চিত্তরঞ্জন ছিলেন রাজনৈতিক বাস্তববাদী এবং প্রচন্ড বিরোধিতার মুখেও তিনি নিজ অবস্থান থেকে কখনও বিচ্যুত হতেন না। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অতি প্রয়োজনিয় দিকটির বাস্তব সমাধানের উদ্দেশ্য তিনি এক বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের আস্থাভাজন হয়ে তাদেরকে নিজের পক্ষে আনার চেষ্টা করেন। এই চুক্তিটিই বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত। ১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত স্বরাজ্য পরিষদ দলের এক সভায় চুক্তিটির শর্তাবলি গৃহীত হয়।
এ সভায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয় যে, প্রদেশে সত্যিকারের স্ব-নিয়ন্ত্রিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই এ চুক্তি কার্যকর হবে। চুক্তিটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ১৯২৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের সভায়ও অনুমোদন লাভ করে। চুক্তিটির বিভিন্ন শর্তের মধ্যে ছিল –
১. বঙ্গীয়-আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব পৃথক নির্বাচক মন্ডলীর মাধ্যমে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।
২. স্থানীয় পরিষদসমূহে প্রতিনিধিত্বের অনুপাত হবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শতকরা ৬০ ভাগ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শতকরা ৪০ ভাগ।
৩. সরকারি চাকরির শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ পদ পাবে মুসলমান সম্প্রদায় থেকে। যতদিন ঐ অনুপাতে না পৌঁছানো যায়, ততদিন মুসলমানরা পাবে শতকরা আশি ভাগ পদ এবং বাকি শতকরা কুড়ি ভাগ পাবে হিন্দুরা।
৪. কোন সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ৭৫ শতাংশের সম্মতি ব্যতিরেকে এমন কোন আইন বা সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা যাবে না, যা ঐ সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বার্থের পরিপন্থী।
৫. মসজিদের সামনে বাদ্যসহকারে শোভাযাত্রা করা যাবে না।
৬. আইন সভায় খাদ্যের প্রয়োজনে গো-জবাই সংক্রান্ত কোন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে না এবং আইন সভার বাইরে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা আনার প্রচেষ্টা চালানো অব্যাহত থাকবে। এমনভাবে গরু জবাই করতে হবে যেন তা হিন্দুদের দৃষ্টিতে পড়ে তা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করে। ধর্মীয় প্রয়োজনে গরু জবাইয়ের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করা যাবে না।
দুঃখের বিষয় যে, বাংলায় কংগ্রেসের অনেক নেতা চুক্তিটির বিরোধিতা করে। এস.এন ব্যানার্জী, বি.সি পাল ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির হিন্দুরা এটির বিপক্ষে অনমনীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাদের ভয় ছিল যে, চুক্তিটি হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রভাব দুর্বল করে ফেলবে। তারা সি.আর দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে, তিনি হিন্দুদের অধিকার বিসর্জন দিয়েছেন। এমনকি অনেক মধ্যপন্থী হিন্দু নেতা মনে করেন যে, সি.আর দাশ মুসলমানদের আস্থা অর্জন করার চেষ্টায় অনেকটা ছাড় দিয়েছেন।
চিত্তরঞ্জন দাশ কিন্তু সকল বিরোধিতার মুখেও অটল থাকেন। চুক্তিটির প্রয়োজনিয়তার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ব্যতীত স্বরাজ সম্ভবপর নয়। তিনি বাংলার বেশ কিছু কংগ্রেস নেতার সমর্থন লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে জে.এম সেনগুপ্ত,কিরণসংকর রায়, সুভাষচন্দ্র বসু, অনিলবরণ রায়, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং প্রতাপচন্দ্র গুহ উল্লেখযোগ্য। তাঁর পরিকল্পনার প্রতি তিনি বাংলার অধিকাংশ মুসলমানের প্রাণঢালা সমর্থন লাভ করেছিলেন। তাঁরা সর্বান্তকরণে চুক্তিটিকে স্বাগত জানান। বাংলার মুসলমানগণ অনুধাবন করেছিলেন যে, চুক্তিটির বাস্তবায়ন সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের মূলে আঘাত হানবে। মুসলিম গণমাধ্যমগুলি তাদের ন্যায্য দাবিসমূহ পূরণ করার মতো ঔদার্য প্রদর্শন করায় হিন্দুনেতাদের ধন্যবাদ জানায়।
কিন্তু ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোকনদ সেশনে চুক্তিটি বাতিল করা হলে তাদের মোহমুক্তি ঘটে। তাদের মতে, কোকনদ কংগ্রেস যে মস্ত ভুল করে সেটি ছিল কংগ্রেস আন্দোলনের ইতিহাসে জঘন্যতম ও এ ভুল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ক্ষেত্রে এবং কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রতি চরম আঘাত হেনেছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে অবস্থান নিয়েছিল, চিত্তরঞ্জন দাশ তার সমালোচনা করে ঘোষণা করেন, “তোমরা সভার সিদ্ধান্তসমূহ থেকে বেঙ্গল প্যাক্টকে মুছে ফেলতে পার, কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস থেকে বাংলাকে বাদ দিতে পারবে না…এ রকম শিষ্টাচারহীন রীতিতে বাংলাকে মুছে ফেলা যাবে না। যারা চিৎকার করে বলে যে ‘বেঙ্গল প্যাক্টকে মুছে ফেল’ তাদের যুক্তি আমি বুঝতে পারি না… বাংলা কি অস্পৃশ্য? এ রকম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করার বাংলার অধিকারকে কি তোমরা অস্বীকার করবে? যদি তোমরা তাই কর, বাংলা তার নিজের ব্যবস্থা নিজেই গ্রহণ করতে পারবে। তোমরা অভিমত ব্যক্ত করার ব্যাপারে বাংলার অধিকারকে প্রত্যাখ্যান করতে পার না”।
১৯২৪ সালে কলকাতা সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন। এ সময়ে তিনি নারী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ ইত্যাদির পক্ষে অনেক কাজ করেন।
ভারতীয় কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করলেও সি.আর দাশ তাঁর শক্তি ও উদ্দেশ্যের সততার বলে ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে চুক্তিটির বিধানসমূহের অনুমোদন লাভের আপ্রাণ চেষ্টা চালান। মাওলানা মহম্মদ আকরম খাঁ এই অধিবেশনের সভাপতি হন। অধিবেশনে প্রায় পনের হাজার প্রতিনিধি যোগ দেন।প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে চুক্তি অধিবেশনে গৃহিত হয়। সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন দাশ বলেন – “হিন্দুরা যদি মুসলমানের মনে আস্থা সৃষ্টি করিতে না পারে, তবে হিন্দু-মুসলিম-ঐক্য আসিবে না। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ব্যতীত আমাদের স্বরাজের দাবি চিরকাল কল্পনার বস্তুই থাকিয়া যাবে”। যদিও ভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক মেনে নিতে অস্বীকার করা হয়েছে, তবু ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন কর্তৃক তিনি চুক্তিটির শর্তাবলি অনুসমর্থন করিয়ে নিতে সক্ষম হন।
দুর্ভাগ্যবশত ১৯২৫ সালে তাঁর অকাল মৃত্যুতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কয়েকজন অনুসারীও চুক্তিটি বর্জন করেন। অনেক বাঙালি মুসলমান রাজনৈতিক নেতা মর্মাহত হন এবং তাঁরা কংগ্রেস ও স্বরাজ্য উভয় দল থেকেই দূরে সরতে থাকেন। মুসলমানদের দলত্যাগের ফলে প্রদেশের উল্লেখযোগ্য কিছু মুসলমান নেতা মৌলভী আব্দুল করিম, মওলানা আব্দুর রউফ, খান বাহাদুর আজিজুল হক, আব্দুল্লা হিল বাকি, মৌলভী আশরাফউদ্দীন, ড. এ সুরাওয়ার্দী, এ কে ফজলুল হক প্রমুখের উদ্যোগে ১৯২৬ সালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি গড়ে ওঠে। যে ঐক্যচিন্তা থেকে চিত্তরঞ্জন তাঁর স্বরাজ্য দলকে নিয়ে এগিয়েছিলেন তা পরিপূর্ণ বিকশিত হতে পারলে শুধু বাংলা নয়, গোটা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসই অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু ইতিহাসে কি হলে কি হত এই সুখকল্পনার মধ্যে কেবল আবদ্ধ থাকার সুযোগ আমাদের নেই। বর্তমানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে বিষবাস্প আমাদের সামনে নতুন ধরনের সংকট নিয়ে এসেছে, আজকের বাস্তবতা অনুযায়ী তার মোকাবিলা করা দরকার। সেই কাজে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের চিন্তা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আমাদের সহায়ক হতে পারে।
দেশদরদী এই নেতা রাজনীতি করতে গিয়ে ব্রিটিশদের রোষানলে পড়ে বহুবার জেল খাটেন। তিনি নারী মুক্তি সমর্থন করতেন এবং নারী-শিক্ষা ও বিধবাদের পুনর্বিবাহকে উৎসাহিত করতেন। তিনি যে অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে ছিলেন তার প্রমাণ মিলে তাঁর নিজ কন্যাদের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবারে বিবাহ দানের ঘটনায়। চিত্তরঞ্জন দাশ সব সময় ব্রিটিশবিরোধী লড়াইকে জোরদার করতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। একসময় তিনি কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে স্বরাজ দল নামের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।
জাতি -বর্ণের বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছিলেন।তিনি নারী মুক্তির সমর্থন করতেন এবং নারীশিক্ষা ও বিধবাদের পুনর্বিবাহকে উৎসাহিত করেন। ১৯২৫ সালে জুন মাসে মাত্র পঞ্চানন বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে বাংলা ও ভারতের সামপ্রদায়িক সমপ্রীতির উপর আঘাত হানে।
১৯২৫ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন শেষে দার্জিলিং যাবার পথে ১৬ই জুন দেশবন্ধু মৃত্যুবরন করেন। মৃত্যুকাৈলে তার বয়স হয়েছিলো ৫৪ বছর। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর পৈতৃক বসতবাড়িটি জনসাধারণের জন্য দান করে যান। সেখানে ‘চিত্তরঞ্জন সেবাসদন‘ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর অকালমৃত্যু বাংলা ও একই সাথে ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর আঘাত হানে।
মাওলানা আবুল কালাম আজাদ মন্তব্য করেছেন যে, ‘তিনি (দেশবন্ধু) অকালে মারা না গেলে দেশে নতুন অবস্থা সৃষ্টি করতেন’। তিনি আরও বলেন,‘পরিতাপের বিষয় এ যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কিছুসংখ্যক অনুসারী তাঁর অবস্থানকে জর্জরিত করে এবং তাঁর ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলে বাংলার মুসলমানরা কংগ্রেস থেকে দূরে সরে যায় এবং (ভারত) বিভক্তির প্রথম বীজ বপন করা হয়’।
তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ/মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান“। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর জীবনানন্দ দাশ তাঁর স্মরণে ‘দেশবন্ধুর প্রয়াণে’ নামক একটি কবিতা রচনা করেন, যা বঙ্গবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি পরবর্তীতে ১৯২৭ সালে জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরা পালকে প্রকাশিত হয়।