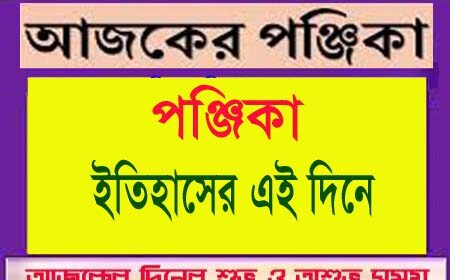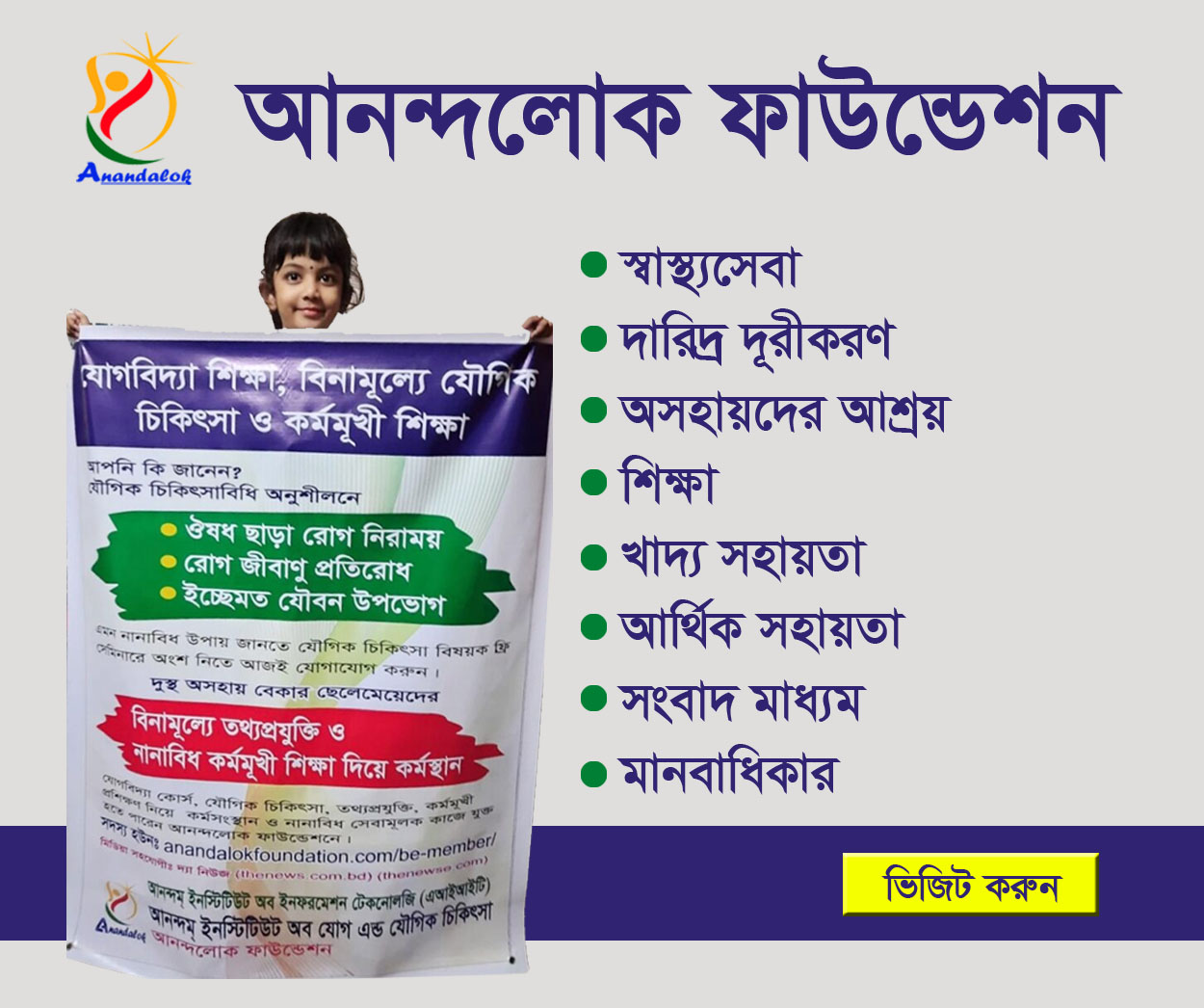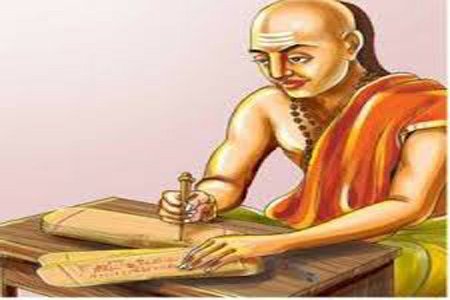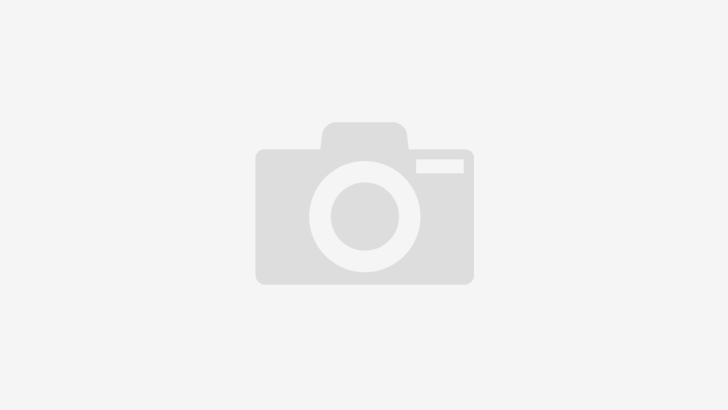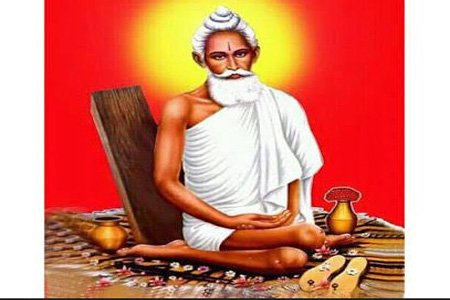আজ শুভ দীপাবলী। শক্তি দেবী মা কালীর পূজা আজ। পুরাণ ও তন্ত্র মতে মা কালীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন, দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, শ্মশানকালী, মহাকালী, রক্ষাকালী ইত্যাদি। আবার বিভিন্ন মন্দিরে ‘ব্রহ্মময়ী’, ‘ভবতারিণী’, ‘আনন্দময়ী’, ‘করুণাময়ী’ ইত্যাদি নামে মা কালী পূজিতা হন। তবে এসব রূপের মধ্যে দক্ষিণাকালীর বিগ্রহই সর্বাধিক পরিচিত ও পূজিতা। তবে মা কালীর যে রূপ আমরা দেখতে পাই বা যে রূপের সঙ্গে আমরা সবচেয়ে বেশি পরিচিত, তা হলো মা কালী কৃষ্ণ বর্ণা, করালবদনী, চতুর্ভূজা, ত্রিনয়নী, দিগম্বরী, মুক্তকেশী, লোহিত জিহ্বা, মুণ্ডমালিনী, শ্বেত দন্তধারীনী, লোহিত জিহ্বাবিভূষিতা। । মায়ের এই যে রূপ কল্পনা করা হয়েছে, তা অকারণ কোনো বিষয় নয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ জগতের সবারই জানা উচিত এই রূপরহস্য।
নিচে শক্তি দেবী মা কালীর রূপ ব্যাখ্যা করা হলো- কালী – ‘কালী’ শব্দের উদ্ভব হয়ে ‘কাল’ থেকে। কাল-এর স্ত্রীলিঙ্গ হলো কালী। কাল বলতে সাধারণভাবে ‘সময়’কে বোঝানো হয়ে থাকে। যিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে কলন করেন, তিনি মহাকাল। আর এই মহাকালের নিয়ন্ত্রক হলেন কালী, যাকে ‘মহাকালী’ অভিধায়ও ভূষিত করা হয়।
কৃষ্ণ বর্ণ – কৃষ্ণ বর্ণ তথা কালো। আমরা আমাদের এই দুচোখ দিয়ে যা দেখি, সবকিছু কিছু না কিছু বর্ণ বা রঙ ধারণ করে। এসব রঙ বা বর্ণই আমাদের চোখের রোডপসিন কোষে প্রতিফলিত হয়ে মস্তিষ্কে বিভিন্ন বর্ণের প্রতিচ্ছবি তৈরি করে। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী মানুষের চোখের ক্ষমতা মেগাপিক্সেল হিসাবে প্রায় ৫৭৬ মেগাপিক্সেল। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও চিত্রগ্রাহক ড. রজার ক্লার্ক (Dr. Roger Clark) এই হিসাবটি দিয়েছেন। এই বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন চোখ দিয়ে মানুষ প্রায় ৬৫ মিলিয়ন রঙের অনুভূতি বুঝতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে মজার বিষয় হলো এতোসব রঙের মধ্যে সাদা এবং কালো রঙ বলতে আমরা যা বুঝি, তা কিন্তু আসলে কোনো রঙ নয়। সাদা রঙ হলো সেটাই যা সব রঙ ফিরিয়ে বা প্রতিফলিত করে দেয় আর কালো রঙ হলো সাদার ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ কালো রঙ সব কিছুই আত্মসাৎ করে বা নিজের মধ্যে বিলীন করে নেয়। এবার আসি, মা কালীর কালো বর্ণের রহস্যভেদে। মা কালী হলো জগজ্জননী। মহাতেজা বিপুল শক্তি ধারণ করে আছেন তিনি। এই শক্তিতে, অর্থাৎ মা কালীর শক্তিতে অপরাপর সকল শক্তিই তথা সর্বভূত বিলীন হয়ে যায় বলেই তিনি কৃষ্ণবর্ণা অর্থাৎ কালো। মা কালীর মহাশক্তির প্রবল তেজ মানুষ স্বচোখে ধারণ করতে পারে না বলেই তিনি কৃষ্ণবর্ণা।
করালবদনী – আগেই বলেছি, মা কালী সকল শক্তিরিই আধার। তার মধ্যে সর্বভূত বিলীন হয়ে যায়। মা কালীই মহাকাল রূপে এই বিশ্বজগত তথা জগতসংসারকে গ্রাস করে নেন, পরে সেই মহাকালকেই গ্রাস করে ফেলেন বলেই তিনি করালবদনী।
চতুর্ভূজা – এই বিশ্বজগত তথা জগতসংসার প্রকৃতপক্ষে শক্তির খেলা মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই বিশ্বজগত চারটি শক্তি দিয়ে পরিচালিত হয়। এই চারটি শক্তি হলো দুর্বল শক্তি, সবল শক্তি, তড়িৎচৌম্বক শক্তি এবং মহাকর্ষ শক্তি। এই শক্তিচতুষ্ঠয় আবার একই শক্তির চারটি রূপ বলে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন আধুনিক বিজ্ঞানের জনক ও বরপুত্র আলবার্ট আইনস্টাইন। ইতোমধ্যেই তার কথার সত্যতা যে দ্ব্যর্থহীন, তা প্রকাশের জন্যই পাকিস্তানের প্রথম নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম প্রমাণ করে গেছেন দুর্বল শক্তি আর তড়িচৌম্বক শক্তি একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র। এভাবেই ধীরে ধীরে আলবার্ট আইনস্টাইনের তত্ত্ব প্রমাণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মা কালী প্রকৃতপক্ষে এই চারটি শক্তিই নিজের মধ্যে ধারণ করে আছেন তাঁর চার হাতে। মা কালীর চার হাত রয়েছে খড়গ, অসুরের ছিন্ন মুণ্ড, বর ও অভয় মুদ্রা। মায়ের চার হাতের এই চারটি রূপ যথাক্রমে খড়গ হলো সবল শক্তি, অসুরের ছিন্ন মুণ্ড হলো দুর্বল শক্তি, বর হলো তড়িৎেচৌম্বক শক্তি এবং অভয় হলো মহাকর্ষ শক্তির প্রকাশক। (প্রতিটি শক্তির সঙ্গে মায়ের হাতের এই যে বর্ণনা, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। পরবর্তী কোনো সময় তা ব্যাখ্যা করা হবে।) মজার বিষয় হলো, বিজ্ঞান যখন প্রমাণ করবে, বিশ্ব পরিচালক এই চারটি শক্তি একই শক্তির চার রূপ, তার মাধ্যমেই প্রমাণ হবে মা কালীর বৈজ্ঞানিক অস্তিত্ব।
ত্রিনয়নী – মানুষ তথা এই বিশ্বজগত প্রকৃতপক্ষে ত্রিকালের অধীন। এই ত্রিকাল হলো ভূত তথা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। এই ত্রিকাল সূর্য, চাঁদ ও অগ্নির মাধ্যমে ত্রিশক্তি হিসেবে প্রকাশিত হয়। মা কালী স্বয়ং এই ত্রিশক্তি ধারণ করেই ত্রিকাল পর্যবেক্ষণ করেন বলেই তিনি ত্রিনয়নী।
দিগম্বরী – এই জগতসংসার মায়ার অধীন। আর মায়া হলো তা-ই, যা বাঁধার সৃষ্টি করে। এই মায়ার বন্ধনেই মানুষসহ সকল জীবই স্ব স্ব জীবন পরিগ্রহ করে। কিন্তু মা কালী তো সকল মায়ার অতীত। তাই কোনো বন্ধনেই তিনি আবদ্ধ নন। একারণেই তিনি আবরণহীনা, দিগম্বরী। আর যেহেতু ‘কাল’থেকে ‘কালী’র উদ্ভব, সেহেতু তা সময় বা কালের সীমানা পেরোনো একটি ধারণা, যা অনন্তকে প্রকাশ করে। এই অনন্তকে কোনো বাঁধন বা আবরণে আবদ্ধ করা যায় না। মা কালী সেই অনন্ত চিন্ময় প্রকাশ, তাই তিনি দিগম্বরী, আবরণহীনা।
মুক্তকেশী – আগেই উল্লেখ করেছি, মা কালী কোনো বন্ধনে আবদ্ধ নন, তিনি মুক্ত। তিনি সব ধরনের বন্ধন, সব ধরনের মায়া থেকেই চিরমুক্ত। মানুষ তাঁকে সাংসারিক বাঁধনে কখনও কখনও বেঁধে ফেললেও তিনি তা থেকেও মুক্ত। আর এই তার এই মুক্ত চরিত্রের প্রকাশই হলো তার মুক্ত কেশ। কেশ মুক্ত থাকলে যেমন তা মাথার সঙ্গে যুক্ত থেকেও তরঙ্গের মতো ঢেউ খেলে ওড়ে, মা কালীও তেমন সমগ্র বিশ্বজগতের সঙ্গে যুক্ত থেকেও মুক্ত, প্রবহমান। তারই প্রতীক মুক্তকেশ। এছাড়াও মুক্ত কেশ বৈরাগ্যের প্রতীকও বটে।
লোহিত জিহ্বা – লাল বর্ণ হলো রঙের মধ্যে সবচেয়ে প্রারম্ভিক পর্যায়ের রঙ। এই রঙ মূলাধার চক্রের রঙ। এই রঙের মানুষের চক্রিক সমন্বয় বা চক্রিক শুদ্ধির প্রক্রিয়া শুরু হয়। অন্যদিকে লাল রঙ হলো রজঃগুণের প্রতীক। তবে লাল রঙের ইতিবাচক গুণ হলো সাহসিকতা, প্রবলতা, উষ্ণতা, শক্তি, উদ্দীপনা এবং উত্তেজনা। অবশ্য লাল রঙের কিছু নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, যেমন- আক্রমণাত্মকতা, আগ্রাসন, মানসিক চাপ ইত্যাদি। এসব বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবে নেতিবাচক মনে হলেও পঞ্চরিপুর বিরুদ্ধে এই গুণগুলোই কিন্তু প্রচণ্ডভাবে ইতিবাচক। মা কালীর মধ্যে এসব গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সবগুলোই প্রকাশমান। এসব বৈশিষ্ট্য বাঙ্ময় করার জন্য মা কালীর জিহ্বার রঙ লাল।
শ্বেত দন্তধারীনী – মা কালী রূপে কালো হলেও, তার দাঁতগুলো উজ্জ্বল সাদা রঙের। এই সাদা রঙ মূলত সত্ত্ব গুণের ধারক ও বাহক। অর্থাৎ এটি সত্ত্বগুণের প্রতীক। সাদা রঙকে প্রায়শই আলো, নিরাপত্তা ও শুচিতার প্রতীক হিসেবে কল্পনা করা হয়। এই রঙ সততা, নির্দোষ অবস্থা ও পবিত্রতার মতো গুণেরও প্রতীক বটে। তবে সাদা রঙের কিছু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন- পরিচ্ছন্নতা, সত্যনিষ্ঠ, শান্তি, শুদ্ধতা, স্বচ্ছতা, সরলতা, নির্দোষিতা ও পবিত্রতা। এই রঙের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য বা গুণ হলো শূন্যতা ও উদাসীনতা। মা কালীর মধ্যে এসব গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সবগুলোই প্রকাশমান। সাদা রঙ ধর্মের পক্ষে যুদ্ধও প্রকাশ করে। মা কালীর প্রতিমায় শ্বেত দন্ত বা সাদা দাঁত দিয়ে লাল জিহ্বাকে আটকে রাখার ব্যাখ্যা হলো সত্ত্ব গুণ দিয়ে রজঃগুণকে আটকে দেওয়া। কেবল মা কালীর পক্ষেই যা সম্ভব।
মুণ্ডমালিনী – মা কালী মুণ্ডমালিনী। এই মুণ্ড ৫০টি মুণ্ড দিয়ে তৈরি হয়। এই মুণ্ড প্রকৃতপক্ষে অহং বিনাশক বা অহং ছিন্ন করার প্রতীক। শুধু তা-ই নয়, এক একটি মুণ্ড এক একটি মাতৃকাবর্ণরূপী বীজমন্ত্রও বটে। এই মূণ্ডমালা বিশ্বজগতের চক্রিক রূপ অর্থাৎ সৃষ্টি আর লয়ের চক্রিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাই মা কালী মুণ্ডমালিনী।
এছাড়াও মায়ের পদতলে থাকেন ত্রিশক্তির আধার শিব। পুরাণ অনুযায়ী, অসুরদের হারানোর পর মা কালী প্রবল বিজয়নৃত্য শুরু করেন। প্রবল এই নৃত্যে নিজেও বিবসনা হয়ে পড়েন। টের পেয়ে অসুরদের কাটা মুণ্ড দিয়ে নিজের কোমরবন্ধনী তৈরি করেন। গড়ে তোলেন গলার মুণ্ডমালা। দেবীর ক্রোধান্বিতা, রণরঙ্গিনী ও করালবদনা রূপে ভীত হয়ে পড়েন দেবতারাও। তাঁদের আশঙ্কা জন্মে, অসুরদের পরে দেবী হয়তো তাঁদেরও গ্রাস করতে পারেন। সেই কারণে ভীত দেবতারা দ্বারস্থ হন মহাদেবের। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য মহাদেব ছুটে যান দেবীর কাছে। কিন্তু মহাদেবের কথা শোনার অবস্থাতেও তখন ছিলেন না দেবী। তিনি তখন উন্মাদিনী। এই পরিস্থিতি দেখে মহাদেব নিজেকে দেবীর পায়ের নিচে স্থাপন করেন। পায়ের নিচে স্বামীর স্পর্শে জ্ঞান ফেরে দেবীর। তিনি লজ্জায় নিজের জিভ কাটেন। দেবীর সেই রূপকেই আরাধনা করা হয় কালী পুজোয়।
পুরানে এমন কথা গল্পচ্ছলে উল্লেখ করা হলেও এর ব্যাখ্যা কিন্তু ভিন্নতর। পুরাণমতে, মহাদেব হচ্ছেন কালীর পতি, স্বামী। কিন্তু এটিও সত্য যে মহাদেব হলেন কাল আর মা হলেন কালী। এই কালের উপর নিজেকে বহমান রাখেন কালী। এই কারণেই সনাতন ধর্মে সকল দেব-দেবীর বাহন থাকলেও কিন্তু মা কালীর কোনো বাহন নেই। কারণ তার কোনো প্রয়োজনও নেই। কারণ নিজেই কালকে তথা নিজের স্বামীকে বাহন করে নিয়েছেন, তার জন্য অন্য কোনো বাহনের কোনো প্রয়োজনই নেই বা হয় না। এটি মানুষের জন্য একটি শিক্ষাও বটে। আর তাই, মা কালীকে কখনও বাবা শিবের পাশে থাকতে দেখা যায় না। বরং শিবের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দেবীরই আরাধনা করেন ভক্তরা। এখানে একটি প্রশ্ন জাগতেই পারে, তবে কেন পা দিয়ে কালের বুকে তিনি দণ্ডায়মান। কেন দেহের অন্য কোনো অঙ্গের স্পর্শ এখানে বিবেচনা করা হলো না। মূলত পা অর্থ স্থিতি। কালের বহমানতায় নিজে স্থিতধী বলেই কাল তথা মহাদেবের উপর মা কালীর পদস্পর্শ বিবেচনা করা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, কোনো বিগ্রহে যদি মা কালীর ডান পা এগিয়ে থাকে, তবে তিনি দক্ষিণাকালী। আর কোনো বিগ্রহে যদি মা কালীর বাম পা এগিয়ে থাকে, তবে তিনি বামা কালী। দক্ষিণা কালী ও বামা কালীর বিগ্রহেরও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। মা কালীর বিগ্রহের আশে-পাশে অসংখ্য ভূত-প্রেত, ডাকিনি-যোাগিনী, শিয়াল ইত্যাদি দেখা যায়। এদের প্রতিটির উপস্থিতি ও অবস্থানই স্বব্যাখ্যাত।